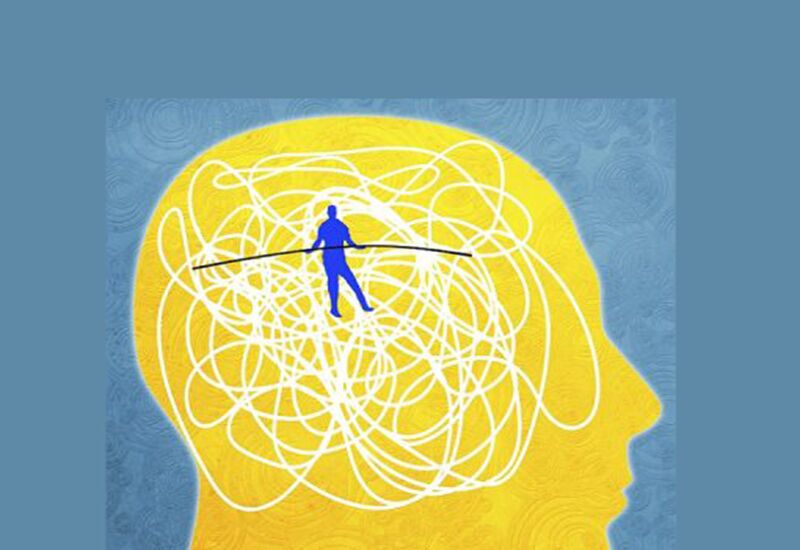লাইক ও ফলো যুগে তরুণ প্রজন্মের মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে খেলা
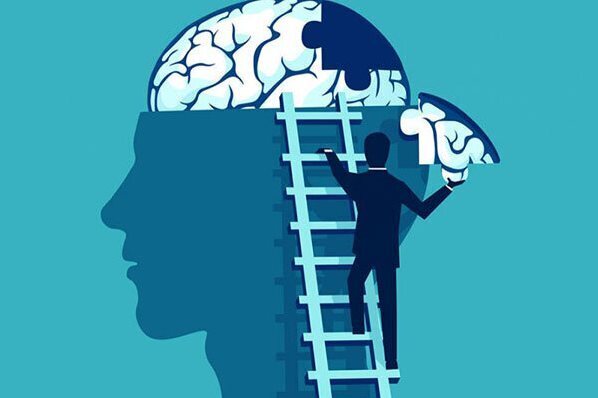
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনার এক নতুন ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু এই সচেতনতার আড়ালে ধীরে ধীরে এক বিপজ্জনক প্রবণতা জন্ম নিচ্ছে — মনোবিজ্ঞানের ভুল ব্যাখ্যা, আত্মনির্ণয়ের (self-diagnosis) প্রচলন, এবং মানসিক ব্যাধিগুলোর স্বাভাবিকীকরণ। মাত্র কয়েক মিনিটের অনলাইন পরীক্ষায় “আপনার কোন মানসিক সমস্যা আছে” বলে ফলাফল দেওয়া বা আবেগভিত্তিক পরামর্শ প্রদানকারী ইনফ্লুয়েন্সারদের কারণে মানসিক স্বাস্থ্য এখন “দেখানোর” এক মাধ্যম হয়ে উঠছে।
মানসিক ব্যাধিকে ট্রেন্ডে পরিণত করা
ভাবুন, সকালে মন খারাপ নিয়ে আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লগইন করলেন। একের পর এক নিখুঁত জীবনযাপনের ছবি, হাস্যোজ্জ্বল মুখ, ফিল্টার করা আলো। হঠাৎ এক ভিডিও আসে—একজন ব্লগার বলছে, “এই তিনটি লক্ষণের মধ্যে দুটি যদি থাকে, আপনি বিষণ্নতায় ভুগছেন।”
এমনই পোস্ট ও ভিডিওর জোয়ারে তরুণরা নিজেদের “বিষণ্ন”, “অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন” বা “মনোযোগহীন” ভাবতে শুরু করছে। বাস্তবে এগুলোর বেশিরভাগই সাময়িক মানবিক অনুভূতি—ক্লান্তি, দুঃখ বা চাপ—যেগুলো এখন মানসিক রোগ হিসেবে ধরা হচ্ছে।
আত্মনির্ণয় থেকে আত্মবিমারগ্রস্ততা
আগে মানসিক অসুস্থতা ছিল এক প্রকার ভয় ও সামাজিক কলঙ্কের বিষয়। কিন্তু এখন অনেকের কাছে এটি একধরনের “ভিন্নতা” বা “গভীর আত্মচেতনা”-র প্রতীক। তরুণদের মধ্যে “আমি হয়তো ADHD রোগী”, “আমার হয়তো বর্ডারলাইন পারসোনালিটি আছে” — এমন মন্তব্য দেখা এখন খুবই সাধারণ।
এই প্রবণতা, যদিও আত্মচেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছিল, এখন তা রূপ নিয়েছে সমষ্টিগত আত্মবিমারগ্রস্ততা (collective hypochondria)-তে। এতে স্বাভাবিক আবেগীয় প্রতিক্রিয়াগুলোকে রোগ হিসেবে দেখা হয়, এবং মানুষ প্রকৃত উন্নতির চেষ্টায় অনাগ্রহী হয়ে পড়ে।
মানসিক স্বাস্থ্য: এক নতুন বাণিজ্য
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য এখন এক লাভজনক বাজার। “দ্রুত আত্মচেতনা”, “তাৎক্ষণিক শান্তি” ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন কোর্স, বই, ও অনলাইন থেরাপি। কিন্তু এর অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিহীন। ফলাফল—আত্মবিশ্বাস হারানো, বাস্তব উন্নতির বদলে মিথ্যা আশা এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি।
বিশেষজ্ঞের মন্তব্য: “মনোবিজ্ঞানের হলুদ প্রবাহ”
এই বিষয়ে ইকনা কথা বলেছে মরিয়ম কাসিরি-র সঙ্গে—তিনি একজন মনোবিজ্ঞানী ও গণমাধ্যমকর্মী। তাঁর মতে,
“আজ মানুষ ইন্টারনেটে যেমন শারীরিক রোগ সার্চ করে, তেমনই মানসিক সমস্যা নিয়েও খোঁজ করে। কিন্তু মন ও মস্তিষ্কের জটিলতা শুধুমাত্র অনলাইন টেস্টে বোঝা সম্ভব নয়। ফলে মানুষ ভুলভাবে নিজেকে অসুস্থ ভাবছে এবং চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে ফেলছে।”
তিনি বলেন, “অনেকে আত্মচেতনার নামে নিজের সমস্যাকে গ্রহণ করে, কিন্তু সমাধানের চেষ্টা না করে সেটিকে নিজের পরিচয়ের অংশ বানিয়ে ফেলে। এতে ব্যক্তিগত উন্নতি থেমে যায়।”

সামাজিক কারণ: গ্রহণযোগ্যতা ও পরিচয়ের খোঁজ
বিশেষত কিশোর ও তরুণদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি। কারণ, তারা সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও গোষ্ঠীগত পরিচয়ের খোঁজে থাকে। কোনো মানসিক লেবেল বা পরিচয় তাদের সেই অনুভূতি দেয়—যে “আমি একা নই, আমি একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অংশ।”
তবে এই আত্মপরিচয় আসলে সমস্যাকে স্থায়ী করে এবং বাস্তব চিকিৎসা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।
নেটওয়ার্কের প্রভাব: “ইনফ্লুয়েন্সার” বনাম “বিশেষজ্ঞ”
সোশ্যাল মিডিয়া একদিকে সচেতনতা ছড়ায়, অন্যদিকে বিভ্রান্তিও তৈরি করে। “মনোবিদ” নামে অনেক ইনফ্লুয়েন্সার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়াই আবেগময় উপদেশ দিচ্ছেন। তাদের জনপ্রিয়তা আসল বিশেষজ্ঞদের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের কথাকেই সত্য মনে করছে।
কাসিরি বলেন, “এই ইনফ্লুয়েন্সাররা মনোবিজ্ঞানী নয়, তারা আসলে ‘মনোবিজ্ঞানের শোম্যান’। মিডিয়া যদি এই ভুয়া বিশেষজ্ঞদের জায়গা না দেয় এবং প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের প্রচার করে, তবে সমাজে সচেতনতা বাড়বে।”
সমাধান: অন্তর্মূল্যবোধ ও ভারসাম্যের শিক্ষা
বর্তমানে তরুণ সমাজ বাহ্যিক স্বীকৃতির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তারা লাইক, কমেন্ট ও ফলোয়ের মাধ্যমে নিজেদের মূল্যায়ন করে। এই নির্ভরতা ধীরে ধীরে অভ্যন্তরীণ শূন্যতা ও আত্মমূল্যবোধের সংকটে পরিণত হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এখনই সময় তরুণদের শেখানোর—নিজেদের ভেতরকার মূল্য ও সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়া, বাহ্যিক প্রশংসায় নয়।

আত্মচেতনা বনাম আত্মকেন্দ্রিকতা
“নিজেকে ভালোবাসো”, “নিজেকে অগ্রাধিকার দাও” — এসব স্লোগান শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু অতিরিক্ত প্রয়োগ মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক ও সহানুভূতিহীন করে তুলছে। প্রকৃত আত্মসম্মান আসে নিজের সীমাবদ্ধতা ও অন্যের অনুভূতি বোঝার মধ্য দিয়ে, শুধুমাত্র “আমি গুরুত্বপূর্ণ” ভাবনা দিয়ে নয়।
আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, মানসিক ব্যাধি হলো এমন একটি অবস্থা যা ব্যক্তির চিন্তা, আবেগ ও আচরণকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই সংজ্ঞা বিকৃত হয়ে গেছে।
আজ অনেক তরুণ “অসুস্থ” না হয়েও নিজেদের “রোগী” মনে করে, এবং এভাবেই আত্মোন্নয়ন থেমে যাচ্ছে।
সত্য হলো — মানসিক স্বাস্থ্য কোনো ট্রেন্ড নয়, এটি জীবনের এক বাস্তব অংশ।
কখনো কখনো, একটুখানি দুঃখ কেবল দুঃখই — কোনো রোগ নয়।
সচেতনতা প্রয়োজন, কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্লেষণ নয়; কখনো কখনো শান্তি আসে বোঝা ও নীরবতায়। 4313485#